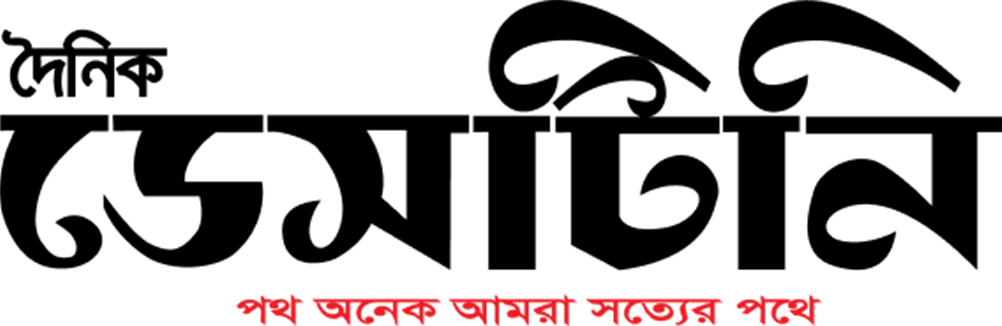

১৯৬৫ সালের ১১ জুন আমেরিকায় শিকাগোর ডব্লিউএফএমটি রেডিওতে বাংলা ভাষার অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রায় এক ঘণ্টার একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। লেখক ও ইতিহাসবিদ স্টাডস টারকেলের নেওয়া সেই সাক্ষাৎকারটিতে গত শতাব্দীর ঘটনাবলি নিয়ে নানান কথা উঠে এলেও বর্তমানের যুদ্ধ-গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে তার কথাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক। আমেরিকা থেকে এ রেডিও সাক্ষাৎকারটি সংগ্রহ করে কালান্তরের পাঠকদের জন্য অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন কবি তুহিন দাস
পর্ব: ৪
স্টাডস টারকেল: আপনার এ কথাগুলো বেশ দুঃখজনক। আমি নিশ্চিত আপনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, সম্ভবত খুব নেতিবাচকভাবে, রাস্তায় দেখা হওয়া সেসব মানুষরাও। আপনি বলছিলেন যে মানবতার কবর অনেক আগেই রচিত হয়েছে। কিন্তু পথের সে লোকটির কর্তৃত্বহীনতা ও অক্ষমতার অনুভূতি রয়েছে। আমাদের ভালো শিক্ষাদানকারীরা আছেন আর আছেন তাদের অনুসারীরা যারা সত্যের সন্ধান করছেন। তারা এ সাধারণ মানবতার কথা বোঝেন, যা আপনি বলছেন। হ্যাঁ, নৃশংসতা সেই ধরনের অমানবিকতা যার কথা আপনি বললেন—তার আকাঙ্ক্ষা আছে ওই মেলার প্যাভিলিয়নগুলোতে। লোকটা জাপানি, ভারতীয় বা ভিয়েতনামীদের দেখে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এ শর্তগুলোতে স্তরের পর স্তর রয়েছে…
অমিয় চক্রবর্তী: এটা আমাদের কাজ। আমি নিশ্চিত যে, আপনিও একই রকম অনুভব করেন যখন আপনি কোনো পক্ষপাত বা প্রোপাগান্ডা ছাড়াই আপনার অদৃশ্য শ্রোতাদের কাছে সত্য প্রকাশ করেন। সংবাদ, রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনার কথার পক্ষে অবস্থান তুলে ধরা একটি দুর্দান্ত কাজ এবং আমরা বলছি না যে আমরা দেশপ্রেমিক নই। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, আমাদের দেশের লোককে ভালোবাসি। কিন্তু সেই গর্বের সঙ্গে অন্য মানুষের অধিকারগুলোর স্বীকৃতিও জড়িত। আমরা এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারি। কীভাবে, আমরা তা জানি না। আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুর্দান্ত কাজ করছে, মনে হয় অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও, যেমন—কোয়েকার, ইউনিটেরিয়ান, প্রধান চার্চগুলো। ধারাবাহিকভাবে ক্যাথলিক চার্চগুলোর দরজা পোপ জনের সময় থেকে (মেয়াদকাল: ১৯৫৮-১৯৬৩) সুন্দর ও প্রশস্তভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। পোপ পল ভারত ভ্রমণ করেছেন (১৯৬৪) এবং তিনি অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি যেখানেই গেছেন সেখানে ৯৮ শতাংশ মানুষ খ্রিষ্টান ছিল না। তিনি ভাবছিলেন কেন তারা আমাকে দেখতে এসেছে? ওহ, আপনি একটি মহান বিশ্বাসের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন, এটা তো এক বিরাট আনন্দের ব্যাপার! তারা অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তার কাছে এটি একটি অসাধারণ ব্যাপার ছিল যে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অন্যের সম্পর্কে এরকম অনুভব করতে পারে। আমাদের কাছে থাকা রেডিও, সংবাদপত্রের মতো বিভিন্ন মাধ্যমেও এটি ঘটছে। সবকিছু একটি মাধ্যমে পাওয়া যায় না—মুদ্রিত বই, লিখিত শব্দমালা, মানুষের সাক্ষাৎ, নিউইয়র্কের বিশ্বমেলা—আমরা মানুষের জন্য যে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারি: একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে গান শোনা, একে অন্যের বাড়িতে আসা-যাওয়া। তবে অবশ্যই আমি জানি আমরা একটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির কথা বলছিলাম। এটা একরকম মন শক্ত হয়ে যাওয়া, ধমনি শক্ত হওয়ার মতো। মানসিক স্থবিরতা শারীরিকভাবে স্থবির হওয়ার রোগের চেয়েও অনেক খারাপ। এর নিরাময় করতে হবে। আমরা কীভাবে আমাদের মনকে একটু চাঙা করতে পারি? সংগীত ও শিল্পের মতো মানবিক অনুষঙ্গের কাছে মনকে তুলে ধরুন। সত্যি বলতে, আমি খুব আশাবাদী, কারণ যখন এসব চলছে তখন নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন শিল্প জাদুঘরে চীনা শিল্পকর্মের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে একটি চলছে এবং সেখানে হাজার হাজার দর্শক চীনা শিল্পের অমর সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিলেন। চীনারা নিজেরা নিজেদের প্রতিন্দ্বন্দ্বী। তারা আসলে অসাধারণ সৌন্দর্য ও শিল্পের স্রষ্টা। এখন তারা বলবে আজকের চীনারা এর চর্চা করছে না। আমি বলব, আপনি কি নিশ্চিত যে চীনাদের সবাই এটা করছে না? তখন বলবে, ওহ, আমি সরকারের কথা বলছি! আমি বলব, ঠিক আছে, তবে আপনি এরই মধ্যে একটি বড় কথা বলে ফেলেছেন! সেখানকার জনসাধারণ কিন্তু আপনার আর আমার মতোই। আমাদের ভুল যখন বোমা হামলার দিকে অগ্রসর হয়, তখন আসলে আমরা শিকারকেই শিকার করছি। যদি সরকার খারাপ হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই দেশের মানুষ। আমরা তাদের কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি? লাখ লাখ মৃত্যু।
স্টাডস টারকেল: আমরা নিজেরা নিজেদেরই শিকার করছি। আবার ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও গান্ধী প্রসঙ্গে। মানুষ হিসেবে তারা পৃথক ছিলেন, কিন্তু তারা ছিলেন একই মানবতায় পূর্ণ। এখন আমরা অনেক দক্ষ, আমাদের এতসব বোমারু বিমান আছে—আপনি জানেন যে আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, আসুন আমরা অতীতের মতবাদগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করি। আমরা কি সেসব দ্বারা মোহগ্রস্ত হই না? আমরা যা যা করে চলেছি তা যদি করেই চলি যেমনটা আপনি বললেন, তাহলে কি আমরা নিজেরা বিলীন হয়ে যাব না?
অমিয় চক্রবর্তী: এটা আমাকে বরিস পাস্তেরনাকের সঙ্গে কাটানো এক গৌরবময় দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মস্কোর পেরেডেলকিনো নামক স্থানে (রাশিয়ায় অবস্থিত, সোভিয়েত লেখকদের বসবাসের জন্য স্থাপিত গ্রামে) তিনি থাকতেন, সেখানে তার মৃত্যুর (মে, ১৯৬০) তিন মাস আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। আর এ মানুষটি ছিলেন এমন একজন যিনি সব ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যেমন নাৎসি আক্রমণ, প্রথম (১৯১৪-১৯১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭, রাশিয়া)। কিন্তু তিনি একজন দয়ালু বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আপনি যদি তার মুখের মায়া দেখতে পেতেন! আমার মনে পড়ছে তার লেখা ‘ডক্টর জিভাগো’ উপন্যাসের শেষে সংযুক্ত তার একটি কবিতা (শিরোনাম ‘ভোর’) যেখানে তিনি প্রথম পুরুষ একবচনে এরকম বলেছেন—আজ সকালে আমি রাস্তায় লোকজনের দিকে তাকালাম, তারা তাদের অফিসে যেতে তাড়াহুড়ো করছে, রাস্তায় প্রচুর তুষার, বাচ্চারা তুষারের বল নিয়ে খেলছে, এখনো অনেকে ঘরে বসে আছেন। তারা আমার থেকেও বিজয়ী যারা ভালোবাসার দ্বারা জয়ী হয়।
মানবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে জয়ী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে প্রকৃত বিজয় নিহিত আছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, যদি আমরা তা না করি, তাহলে এর উল্টোটা ঘটে। আমরা অন্যের ওপর বিজয়ী হচ্ছি, কিন্তু পরাজিত হচ্ছি ঘৃণার কাছে। আমরা যে সত্য ধারণ করি, তার মাধ্যমে উন্নত হওয়ার বদলে, আমাদের মধ্যে থাকা মন্দতায় ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছি। এর জন্য সবচেয়ে কঠিন মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং অনেক মানুষ জানে না যে তারা কী মূল্য পরিশোধ করছে। তারা শুধু নিজেরাই নয়, বরং শিশুদেরও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য করছে। আপনি যদি কার্টুনের পৃষ্ঠাগুলো দেখে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে সন্দেহজনক চরিত্র ও খারাপ মানুষদের চিবুকের হাড়গুলো মঙ্গোলিয়ানদের মুখের মতো উঁচু, আপনি প্রায়ই এটি দেখতে পাবেন। এমন আবহ সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট জাতিকে মানবজাতির প্রধান শত্রু হিসেবে একটি ভাবমূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। এই শিশুদের ছড়া ও পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। জার্মানরা ও ফরাসিরাও একে অন্যের সঙ্গে এটি করেছিল, তারা শিশুদের পাঠ্যবইয়ে এসব অদ্ভুত ধারণা ঢুকিয়েছে। তাহলে এখন কাদের পরাজিত করছে? উত্তর প্রজন্মকে। বাচ্চারা যে দুধ খাচ্ছে, তাতে তারা এক ফোঁটা বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। এখন এটা ওদের মেরে ফেলছে না, কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের বিবেক ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের সন্তানদের, নিজেদের, দেশের নাগরিকদের জন্য কি আমরা কেউ এই মূল্য দিতে চাইব? আপনার কথাটা আমি খুবই গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি। চূড়ান্ত পরাজয় হলো মন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করা ও আমাদের মনুষ্য-স্বভাবকে হ্রাস করা। আমরা যতই কার্যকরী হই না কেন, ট্রিগার টানার বা বোতাম টেপার কথা আমরা চিন্তা করি। আসলে আনন্দ করার আর কিছু নেই, কারণ ওই বোতামটিতে চাপ পড়লেই হয়তো আমার মতো অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হবে। এ ধরনের ঘটনার এই দৃশ্যে আমি কি আনন্দ পেতে পারি? এমনকি এমন একটি ঘটনার সম্ভাবনা দেখেও। আমি জানি পৃথিবীর কোথাও মানুষ এত খারাপ নয়। তারা এটা চায় না, কিন্তু তারা নিজেদের এমন একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেছে যখন তারা মনে করে ‘এটা একটি প্রয়োজনীয় মন্দ’। আমি এ বাক্যাংশটির বিরোধিতা করি। যদি এটি মন্দ হয়, তবে এটি প্রয়োজনীয় হতে পারে না।
স্টাডস টারকেল: যেমনটা আপনি বললেন, আপনার প্রসঙ্গে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে, ম্যাক্স ফ্রিডম্যান নামে একজন লেখক আছেন যিনি শিকাগো ডেইলি নিউজ পত্রিকায় লিখে থাকেন এবং আমার মনে হয় ফ্রিডম্যান ওয়াশিংটন থেকে লেখেন। তার লেখার নিজস্ব রচনাশৈলী রয়েছে। তিনি লুইস মামফোর্ডকে আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য নিন্দা করেছেন, যিনি হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিতব্য শিল্প-সাহিত্য উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
অমিয় চক্রবর্তী: রবার্ট লোওয়েল একাডেমিতে (আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস) ভাষণ দিয়েছিলেন এবং একই কথা বলেছিলেন। (ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালের ১৪ জুন প্রেসিডেন্টের বাসভবনে অনুষ্ঠিত আর্টস ফেস্টিভ্যাল কিছু আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার জন্য বিখ্যাত কবি রবার্ট লোওয়েল তখন ছিলেন আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারসের প্রেসিডেন্ট)। [চলবে]
মন্তব্য করুন