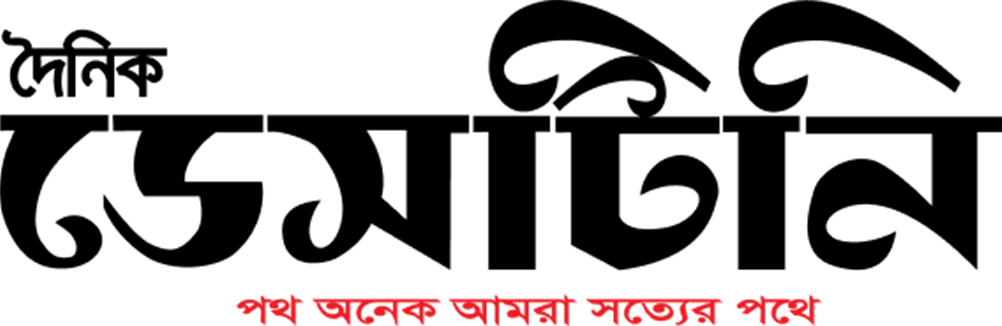
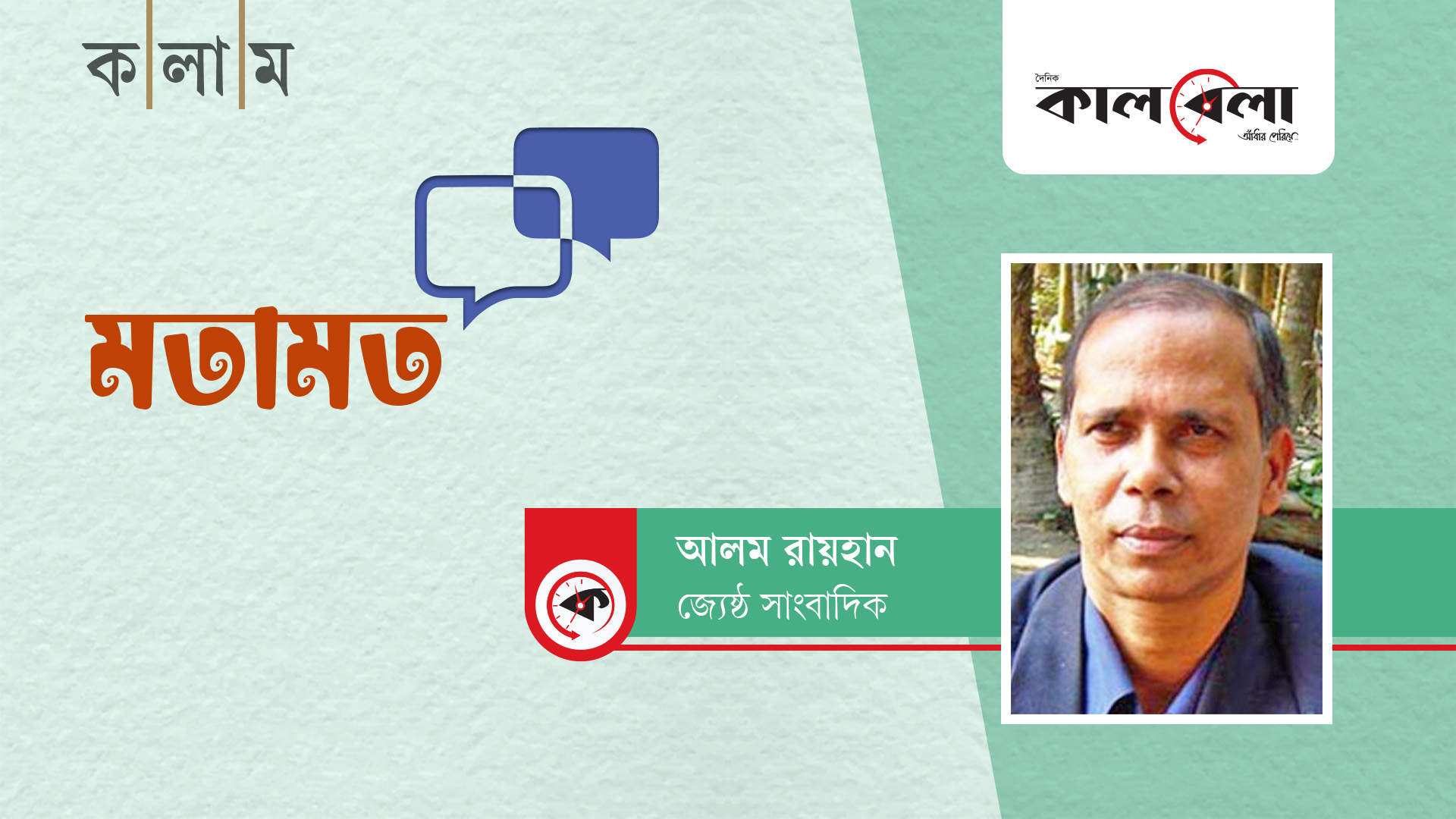
বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী কাজী জাফর আহমেদকে প্রথম দেখেছি বরিশালের অশ্বিনী কুমার টাউন হলে, বেশ খানিকটা দূর থেকে। তিনি মঞ্চে, আমি উল্টো দিকে পেছনে। তখন তিনি ইউপিপি প্রধান। এক দলের ‘এক নেতা’। একই সময় টাউন হলের দোতলায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দেখেছি মজিবর রহমান সরোয়ারকে। সম্ভবত ইউপিপি দিয়ে তার রাজনৈতিক ফাউন্ডেশনের সূচনা। প্রসঙ্গত, বরিশাল বিএনপির যে দুই নেতা কখনো দলত্যাগ করেননি, তাদের মধ্যে মজিবর রহমান সরোয়ার একজন। জিয়া সরকারের সোয়া তিন মাস মেয়াদে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে কাজী জাফরকে দ্বিতীয়বার দেখেছি ১৯৭৮ সালে বরিশাল কলেজ চত্বরে, তমালতলায়। খানিকটা কাছ থেকে। তখন আমি জাসদ ছাত্রলীগের বরিশাল জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক। দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল, কলেজ চত্বরে সামরিক শাসকের শিক্ষামন্ত্রীকে ধাওয়া দেওয়া হবে। টিম লিডার ছিলেন তিমির দত্ত। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। ফলে তার নাটকীয় ভঙ্গিমার ভাষণ শুরুর ক্ষণিক পর আমরা কলেজ চত্বর ত্যাগ করি। তৃতীয়বার তাকে দেখেছি ঢাকার মগবাজারে কাজীর গলিতে তার বাসায়, কাছ থেকে। আমার পেশাগত জীবনের সূচনা পত্রিকা সাপ্তাহিক জনকথার সম্পাদক ইব্রাহিম ভাই (ইব্রাহিম রহমান) আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্পাদকের লক্ষ্য ছিল, অতি নবীনকে সাংবাদিকতায় ধাতস্থ করা। যেমন আগে গ্রামে গরুর গলায় কলাগাছ বেঁধে হাঁটানো হতো, লাঙল টানতে অভ্যস্ত করার জন্য। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ’৭৮ সালে ধাওয়া দেওয়ার হটকারী অ্যাসাইনমেন্টের টার্গেট কাজী জাফরকে অধিকতর কাছ থেকে দেখা। তখনো তার প্রতি আমার নেতিবাচক ধারণা ছিল প্রবল। যদিও অনেক পরে বুঝেছি, আমার ধারণা ছিল ভুলে ভরা। আরও পরে বুঝেছি, একজন রাজনীতিককে চট করে পরিমাপ করা যায় না। ভিন্ন প্রসঙ্গ থাক। আমরা বাধাহীনভাবে কাজী জাফর আহমেদের বাসার ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। তখন রাত ৮টা-সাড়ে ৮টা হবে। তিনি একা বসেছিলেন। মনে হলো বাইরে যাবেন, অথবা বাইরে থেকে এসেছেন। জনকথা সম্পাদককে দেখেই বললেন, ‘ও, ইব্রাহিম আসো। তোমার জন্যই অপেক্ষায় আছি। বাইরে যাব।’ কোনো গৌরচন্দ্রিকায় না গিয়ে ইব্রাহিম ভাই বললেন, জাফর ভাই খবর কী, কী করবেন। কাজী জাফর আহমেদ বললেন, ‘শোনো ইব্রাহিম, তোমাকে একটা চীনা গল্প বলি।’ এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন, ‘নির্জন এলাকা দিয়ে এক তরুণী যাচ্ছিল। মাঝপথে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাকে ঘিরে ধরল। লক্ষ করল, পালাবার পথ নেই! আর নির্জন এলাকায় কেউ রক্ষা করতে আসারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় শি ডিসাইডেড টু এনজয়, বাট নট টু বি রেপড।’
এই বলে কাজী জাফর উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এই ছেলে তুমি মিষ্টি খাও।’ অবশ্য, এ কম্ম আমি আগেই করেছি চীনা গল্প শোনার চেয়ে বেশ মনোযোগ সহকারে। হয়তো এটি লক্ষ করেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। এক ধরনের মমতাবোধ থেকে হয়তো। রাজনীতিকের চোখ এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দীর্ঘ পথচলায় অর্জিত হয়!
রিকশায় উঠে ইব্রাহিম ভাইকে বললাম, জাফর ভাই কী বললেন? কোনো আগামাথাই তো বুঝলাম না! কোনো উত্তর না দিয়ে ইব্রাহিম ভাই স্বভাবসুলভ একটু হাসির ভাব করলেন। সবসময়ই তার হাসিই ছিল অনেকটা মোনালিসার মতো। আমার সন্দেহ হলো, হয়তো তিনি নিজেই কিছু বোঝেননি। আমার মতো নবীনকে আর কী বোঝাবেন! কিন্তু দুদিন পর আমার ভুলের ওপর বজ্রপাতের মতো ঘটনা ঘটল। দৈনিক ইত্তেফাক আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ইব্রাহিম ভাই বললেন, ‘এইবার চীনা গল্পের মাজেজা বুঝলা, বরিশাইল্লা?’ দেখলাম, জেনারেল এরশাদের দলে কাজী জাফর আহমেদের যোগদানের খবর। আবার যেনতেন যোগদান নয়। একেবারে নিজের দল বিলুপ্ত করে যোগদান। নিজের মস্তক কেটে দেবতার চরণে নৈবেদ্য দেওয়ার মতো। তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ল, ফাঁদে পড়া শিয়ালের লেজ কেটে প্রাণ বাঁচানোর গল্পটি। সবাই জানেন, রাজনীতিকদের লেজ কাটার ক্ষেত্রে জেনারেল এরশাদ সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখিয়েছেন। আর এর মনুমেন্ট হয়ে আছেন আতাউর রহমান খান। বলা হয়, তার লেজ কাটা হয়েছে একেবারে গোড়া ঠেকিয়ে।
কাজী জাফর আহমেদের রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ। তার আত্মজীবনীমূলক বইয়ের নাম ‘আমার রাজনীতির ৬০ বছর জোয়ার-ভাটার কথন’। যে বইটি তিনি লেখা শুরু করেন অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসাধীন থাকাকালে ২০০৩ সালে। তখন তার দুটি কিডনিই অচল।
রাজনীতিতে বাম ধারার চলার পাট চুকিয়ে ইউটার্ন দিয়ে প্রথমে সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, পরে আরেক জেনারেলের হাত ধরে উপপ্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন কাজী জাফর আহমেদ। ফলে চীনা গল্পের বাস্তবতায় সফল উদাহরণ হয়েই থাকবেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাজী জাফরই কি একমাত্র মডেল? অবশ্যই না। বরং এ ধারায়ই চলে আসছে রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ। ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহস করে নিজের ভাবনা প্রকাশের মানুষ কমতে কমতে যেন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সবাই এখন সূর্যমুখী। যারা মননে সদাই লালন করেন, ‘টু এনজয়, নট টু বি রেপড।’ এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। কাজেই যেখানে ক্ষমতা সেখানেই অন্যরকম প্রবণতা জাতীয় মজ্জায় সংক্রমিত জেঁকে বসেছে। এখন অনেকেই মোরগ দেখলে যুবতী মুরগির প্রবণতার মতো আচরণ করেন!
এই শ্রেণির মানুষের কারণেই দেশে লুটের ধারা থামছে না। চলছে প্রকল্পের আড়ালে সাগর চুরি। কোনো কোনো সময় চিহ্নিতও হয়েছে, কিন্তু রহিত হয়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব দুর্নীতি করার একটি সূক্ষ্ম কৌশল। প্রকল্প তৈরিতেই দুর্নীতির পথ এমনভাবে রাখা হয়, যা বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে ভাগবাটোয়ারায় কোনোই বেগ পেতে হয় না। বলতে গেলে বিভিন্ন পক্ষ মিলেই চুরির সুযোগ রাখার কৌশল করা হয়। একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আসার আগে কয়েক ধাপ পার হতে হয়। তবে রহস্যজনক কারণে এসব অপকৌশল কোনো ধাপেই ধরা পড়ত না। প্রকল্প প্রস্তাবে পণ্যের দাম বেশি ধরার মধ্য দিয়েই দুর্নীতির বিসমিল্লাহ হয়। একটি প্রকল্প প্রস্তাবে একটি বালিশের দাম ধরা হয়েছে ২৭ হাজার টাকা, বালিশ কাভারের দাম ২৮ হাজার টাকা। আবার একজন ক্লিনারের মাসিক বেতন ধরা হয়েছিল ৪ লাখ টাকা। আরেকটি প্রকল্পে একটি স্যালাইন স্ট্যান্ডের দামই নির্ধারণ হয়েছে ৬০ হাজার টাকা। নদী ড্রেজিং প্রকল্পে সাইনবোর্ড স্থাপনে একেকটির খরচ ২ লাখ টাকা। কফি ও বাদাম চাষে ১০ কর্মকর্তার বিদেশ সফর, সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পে ২ কোটি টাকায় বাংলো নির্মাণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে ৪ কোটি টাকার অডিও-ভিডিও এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাবও এসেছিল। ফলে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকল্প-সংশ্লিষ্টদের বয়ান, ভুল করে এমন প্রস্তাব যায় পরিকল্পনা কমিশনে। পরে সমালোচনা ও পরিকল্পনা কমিশনের চাপের মুখে এসব প্রস্তাব থেকে কদাচিৎ সরেও আসে। কিন্তু যারা কথিত ‘ভুল’ করেন বা ইচ্ছা করে এমন সুযোগ রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। কোনোটিতে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চললেও তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। সাধারণ পণ্যেরই দাম নির্ধারণের এ কাণ্ড করা হয়। অন্যান্য দামি পণ্যের দাম কোথায় ঠেকানো হয়, তা সহজেই অনুমেয়। আর আনুমান করতেইবা হবে কেন? বিতারিত হাসিনা সরকারের আমলের ফিরিস্তি তো এখন বর্তমান সদাশয় সরকারের হাতেই আছে। কিছু কিছু খবর গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল, প্রকল্পের নামে রাষ্ট্রের টাকা লোপাটকারীদের আইনের আওতায় আনা। কিন্তু তা হয়েছে বলে জানা যায়নি। উল্টো আমাদের সদাশয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন, যা শুধু ব্যক্তির ওপর বর্তায় না, দায় চাপে খোদ সরকারের ওপরই।
পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের আমলে উন্নয়নের নামে প্রকল্প বাস্তবায়নে লাগামহীন দুর্নীতি ছিল ওপেন সিক্রেট। প্রকল্প প্রস্তাব মানেই লুটপাটের উদার জমিন। খেয়াল-খুশিমতো ধরা হতো বিভিন্ন পণ্যের দাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলোমেলো প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কারণ মিথ্যাকে সত্যের মতো গুছিয়ে উপস্থাপনার দক্ষতা অথবা ধৈর্য ছিল না হয়তো। বছরের পর বছর এমন ঘটনা ঘটলেও দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কোনো নজির নেই। ফলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ফ্যাসিস্ট শাসনামল জুড়েই। আর যাদের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তারাই ছিলেন এসব দুর্নীতির ভাগীদার। এখনো তাইতো আছেন। গ্রামে একটা কথা আছে—‘আমরা আর মামুরা’। হয়তো এর অনুকরণ করা হয়েছে গ্রামীণফোনের বিজ্ঞাপনে, ‘আমরা আমরাই তো...’।
এদিকে মসনদে থেকেও অবলীলায় ছাত্রদের ‘নিয়োগ কর্তা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার দশ মাসের মাথায়, ক্যালেন্ডার গুনে হিসাব করলে দশ মাস দশ দিনও হতে পারে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে রাজনীতির ক্ষমতা কেন্দ্রের সঙ্গে বখেদমতে হুজুরে আলা সহাস্যে করমর্দন করে এসেছেন। যেন কত আপন! কিন্তু এতে তার কথিত নিয়োগকর্তারা গোস্বা করেছেন। উষ্মা প্রকাশ করেছেন জুলাই-আগস্টের পটপরিবর্তনের অন্যতম নেপথ্য শক্তি জামায়াতও। এ পুরো বিষয়টিকে রাজনীতির খেলাধুলা হিসেবে আখ্যায়িত করে পার পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা উপদেষ্টা যখন বলেন, ‘অস্থিরতার শঙ্কায় প্রকল্পে কর্মকর্তাদের বাড়তি সুবিধা কমানো যাচ্ছে না।’ তখন সান্ত্বনা খোঁজার আর কি কোনো অবকাশ থাকে?
প্রসঙ্গত, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ২১ জুন বলেছেন, ‘নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, এমন শঙ্কায় উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরতদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা কমানো যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্প ব্যয় কমিয়ে আনার চেষ্টা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পে দুর্নীতি ও অযাচিত খরচ কমানো গেলে বাজেটে পরিচালন ব্যয় অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। আগের সরকারের সময়ে টেন্ডার যোগসাজশেই প্রকল্পে ১০ শতাংশ দুর্নীতি হতো। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উপকারভোগীর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই ভূতুড়ে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকায় ঢুকেছে।’
প্রকল্প বিষয়ে যাদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা তারাই দুর্নীতি বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এবং সততা দক্ষতার প্রমাণিত প্রতীক এম এ মান্নান ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ই বলেছিলেন, ‘অতিরিক্ত ব্যয় বা ভুল ব্যয় প্রস্তাব কখনো কাম্য নয়। যারা এরকম ব্যয় প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা উচিত। এটা করা না গেলে বারবার একই ভুল হতেই থাকবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চেয়েছিলাম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো যাতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়। আমার জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করেছি।’ বলা বাহুল্য, তার ‘চেষ্টা’ সফল হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ তার মাথার ওপর যিনি ছিলেন, তিনি তো লুটের মহারানি হিসেবে খ্যাত। তাকে নিয়ে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সাংবাদিক রেজা রায়হানের একটি বইয়ের নাম, ‘দুর্নীতি কন্যা’। দুর্নীতির কন্যার সময় লুট হওয়ার বিষয়টি জায়েজ হিসেবে বিবেচনার পক্ষে নিশ্চয়ই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার লোক আছে। কিন্তু ৫ আগস্টের পর তো আগের অবস্থা থেকে ইউটার্ন করা কথা ছিল। কিন্তু তা কি হয়েছে! বর্তমান পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের অসহায় উচ্চারণ কী প্রমাণ করে?
পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকার কাঠামোতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি কোনো প্রেক্ষাপটেই ‘কথার কথা’ বলার লোক নন। এ কারণেই তার এই উচ্চারণ আবার মনে করিয়ে দেয়, কাজী জাফরের মুখে অনেক আগে শোনা চীনা গল্পটি। সেই গল্পের ভিত্তিতে চাইলে নতুন আপ্তবাক্য রচনা করা চলে, ‘ধর্ষিত হওয়ার চেয়ে উপভোগ শ্রেয়!’ কিন্তু এ ধারা আমাদের দেশ কদিন চলবে, আমরা কোথায় যাচ্ছি? হায় কপাল!
লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
মন্তব্য করুন